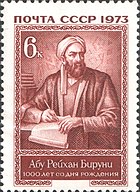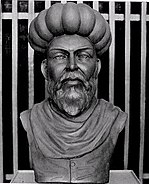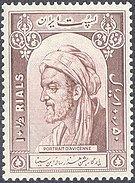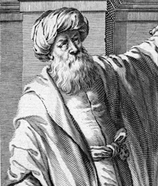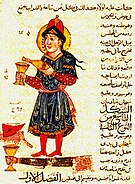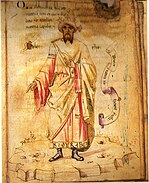ইসলামি স্বর্ণযুগ
ইসলামের ইতিহাসে অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে ইসলামের স্বর্ণযুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সময়ে মুসলিম বিশ্ব ব্যাপক বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সাধন করেছিল।[১][২][৩]
| অষ্টম শতাব্দী – চতুর্দশ শতাব্দী | |
| পূর্ববর্তী যুগ | রাশিদুন খিলাফত |
|---|---|
| পরবর্তী যুগ | তিমুরিদ রেনেসাঁ বারুদ সাম্রাজ্য |
| শাসক(গণ) | উমাইয়া খিলাফত, আব্বাসীয় খিলাফত, সামানি সাম্রাজ্য, ফাতিমীয় খিলাফত, আইয়ুবীয় রাজবংশ, মামলুক সালতানাত |
| নেতা(গণ) | |
ঐতিহ্যগতভাবে, ধারণা করা হয় যে এই সময়কালের সূচনা ঘটেছিল আব্বাসীয় খলিফা হারুন-আল-রশিদের (৭৮৬-৮০৯ খ্রিস্টাব্দ ) শাসনামলে। তখন 'জ্ঞানের ভবন' (House of Wisdom) প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র থেকে পণ্ডিতরা বাগদাদে আসতে থাকেন। বাগদাদ তখন পৃথিবীর বৃহত্তম শহর ছিল। পণ্ডিতরা এসে তৎকালীন জগতের প্রাচীন শাস্ত্রীয় জ্ঞানকে আরবি ও ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন।[৪] মঙ্গোলদের আক্রমণ ও ১২৫৮ সালের বাগদাদ অবরোধের ফলে আব্বাসীয় খলিফার পতন ঘটলে এই স্বর্ণযুগের সমাপ্তি ঘটে বলে ধরে নেয়া হয়।[৫]
তবে এই স্বর্ণযুগের সময়কাল নিয়ে বিকল্প ধারণাও রয়েছে। কিছু পণ্ডিত তিমুরীয় রেনেসাঁ-কে স্বর্ণযুগের অংশ ধরে এর সময়কাল ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত করেন।[৬][৭] আবার কেউ কেউ ১৫শ-১৬শ শতক পর্যন্ত সময়কাল, যখন ইসলামি বারুদ সাম্রাজ্যগুলোর উত্থান হয়েছিল, সেসময় পর্যন্ত ইসলামি স্বর্ণযুগের অংশ বলে মনে করেন।[১][২][৩]
ধারণার ইতিহাস
সম্পাদনাউনিশ শতকে ইসলামি ইতিহাসের সাহিত্যে স্বর্ণযুগ রূপকের ব্যবহার শুরু হয়, যেসময়ে 'প্রাচ্যবাদ' (Orientalism) নামে পরিচিত এক পশ্চিমা নান্দনিক ধারার জনপ্রিয়তা ছিল। ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত "হ্যান্ডবুক ফর ট্র্যাভেলার্স ইন সিরিয়া অ্যান্ড প্যালেস্টাইন"-এর রচয়িতা উল্লেখ করেন যে দামেস্কের সবচেয়ে সুন্দর মসজিদগুলো, "মুহাম্মাদি ধর্মের মতোই এখন দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে" এবং এগুলো "ইসলামের স্বর্ণযুগের" নিদর্শন।
এই ধারণাটির কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই, আর সাংস্কৃতিক বা সামরিক অর্জনের উপর বেশি গুরুত্ব রাখা হয় তার উপর নির্ভর করে এর সময়কালে পার্থক্য হতে পারে। যেমন, একজন উনিশ শতকের লেখক এই যুগকে খিলাফতের পুরো সময়কাল অর্থাৎ "সাড়ে ছয় শতাব্দী" ধরে বিস্তৃত বলে উল্লেখ করেন; অন্য আরেকজন লেখক রাশিদুন খলিফাদের বিজয় এবং খলিফা উমরের মৃত্যু ও প্রথম ফিতনার কয়েক দশকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান।
বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, এই শব্দটি খুব কমই ব্যবহৃত হত এবং প্রায়শই একে রাশিদুন খলিফাদের প্রাথমিক সামরিক সাফল্য হিসেবে বর্ণনা করা হত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসেই এই শব্দটি ঘনঘন ব্যবহৃত হতে শুরু করে; তখন মূলত নবম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত খিলাফতের শাসনামলে বিজ্ঞান ও গণিতের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিকে (হাউস অব উইজডমের প্রতিষ্ঠা এবং ক্রুসেডের সূচনার মধ্যবর্তী সময়কাল) বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। তবে অনেক সময় অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ বা দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যাই হোক, এখনও এই সময়সীমার সংজ্ঞা পণ্ডিতদের মধ্যে বেশ তারতম্যপূর্ণ।
খিলাফতের অবসানের সাথে স্বর্ণযুগের সমাপ্তিকে তুলনা করা ঐতিহাসিকভাবে একটি সুবিধাজনক বিরতি বিন্দু। কিন্তু একথাও বলা যায় যে ইসলামি সংস্কৃতির ক্রমশ অবনতির সূচনা আরও অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। যেমন, খান (২০০৩) মনে করেন ৭৫০ থেকে ৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী দুই শতাব্দীই হলো প্রকৃত স্বর্ণযুগ। তিনি যুক্তি দেখান যে হারুন আর-রশিদের শাসনামলে অঞ্চলসমূহ হারানো শুরু হয়, আল-মামুনের মৃত্যুর পর ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে চলে যায়। বারো শতকের ক্রুসেডগুলোর ফলে ইসলামি সাম্রাজ্যের দুর্বলতা প্রকট হয়, এবং তা থেকে সাম্রাজ্য আর সেরে উঠতে পারেনি।
স্বর্ণযুগের সমাপ্তি নিয়ে মোহাম্মদ আবদুল্লাহর 'অবনতি তত্ত্ব' (Decline Theory): অষ্টম এবং নবম শতাব্দীর মধ্যে গ্রীকদের প্রাচীন বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ অর্জন ও অনুবাদের একটি বিশাল প্রচেষ্টার মাধ্যমে স্বর্ণযুগের সূচনা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। অনুবাদের এই যুগের পরে ছিল মৌলিক চিন্তাধারা এবং অবদানের দুটি অসাধারণ শতাব্দী, যে যুগটিকে ইসলামি বিজ্ঞানের "স্বর্ণযুগ" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ধারণা করা হয় এই তথাকথিত "স্বর্ণযুগ" নবম শতাব্দীর শেষ থেকে একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এই সময়ের পরবর্তী যুগকে প্রচলিতভাবে 'অবনতির যুগ' বলা হয়। উনিশ শতক থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময়ের সাহিত্যের একটি জরিপ প্রদর্শন করে যে 'অবনতি তত্ত্ব' সাধারণ একাডেমিক পরিসরে একটি পছন্দের প্রতিমানে পরিণত হয়েছে।
তথ্যসূত্র
সম্পাদনা- ↑ ক খ Saliba, George (১৯৯৪)। A History of Arabic Astronomy: Planetary Theories During the Golden Age of Islam। New York University Press। পৃষ্ঠা 245, 250, 256–257। আইএসবিএন 0-8147-8023-7।
- ↑ ক খ King, David A. (১৯৮৩)। "The Astronomy of the Mamluks"। Isis। 74 (4): 531–55। এসটুসিআইডি 144315162। ডিওআই:10.1086/353360।
- ↑ ক খ উদ্ধৃতি ত্রুটি:
<ref>ট্যাগ বৈধ নয়;Hassan-Declineনামের সূত্রটির জন্য কোন লেখা প্রদান করা হয়নি - ↑ Gutas, Dimitri (১৯৯৮)। Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early 'Abbāsid Society (2nd-4th/8th-10th Centuries)। London: Routledge।[পৃষ্ঠা নম্বর প্রয়োজন]
- ↑ Islamic Radicalism and Multicultural Politics। Taylor & Francis। ১ মার্চ ২০১১। পৃষ্ঠা 9। আইএসবিএন 978-1-136-95960-8। সংগ্রহের তারিখ ২৬ আগস্ট ২০১২।
- ↑ "Science and technology in Medieval Islam" (পিডিএফ)। History of Science Museum। সংগ্রহের তারিখ ৩১ অক্টোবর ২০১৯।
- ↑ Ruggiero, Guido (১৫ এপ্রিল ২০০৮)। A Companion to the Worlds of the Renaissance, Guido Ruggiero। John Wiley & Sons। আইএসবিএন 978-0-470-75161-9। ৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৭ নভেম্বর ২০১৬।