বনু সাকিফ
বনু সাকিফ (আরবি: بنو ثقيف) ছিল একটি আরব গোত্র যারা সৌদি আরবের তায়েফ শহরে এবং এর আশেপাশে বসতি স্থাপন করেছিল। বর্তমানেও এই অঞ্চল তাদের আবাসস্থল। প্রাক-ইসলামী যুগ থেকেই ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
| Banu Thaqif بنو ثقيف | |
|---|---|
| Arabs | |
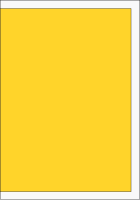 Banner of the Banu Thaqif from the Battle of Siffin | |
| নৃগোষ্ঠী | Arab |
| নিসবা | Thaqafi (الثقفي) |
| অবস্থান | Ta'if, Saudi Arabia |
| এর বংশ | Hawazin, Qays |
| ভাষা | Arabic |
| ধর্ম | Islam |
ইসলাম-পূর্ব যুগে, বনু সাকিফ মক্কার কুরাইশ গোত্রের সাথে বাণিজ্য এবং ভূমি মালিকানায় সমান অংশীদার ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। গোত্রটি প্রাথমিকভাবে ইসলামী নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু ৬৩০ সালে তায়েফ অবরোধের পর তারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিতে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। বনু সাকিফ গোত্রের আন্তঃগোত্রীয় যোগাযোগ এবং তাদের তুলনামূলক উচ্চ শিক্ষা তাদের নতুন মুসলিম রাষ্ট্রে দ্রুত অগ্রগতি করতে সাহায্য করেছিল। ইরাক বিজয় ও শাসনের ক্ষেত্রে তারা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, রাশিদুন ও উমাইয়া খলিফাদের জন্য দক্ষ এবং শক্তিশালী গভর্নর সরবরাহ করে।
ইরাকের উল্লেখযোগ্য গভর্নরদের মধ্যে ছিলেন আল-মুগিরা ইবনে শুবা (৬৩৮, ৬৪২-৬৪৫), জিয়াদ ইবনে আবিহি (৬৬৫-৬৭৩), এবং আল-হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ (৬৯৪-৭১৪)। প্রধান সাকাফি সেনাপতিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন উসমান ইবনে আবি আল-আস, যিনি ৬৩০-এর দশকে প্রথম মুসলিম নৌ অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, মুহাম্মদ ইবনে আল-কাসিম, যিনি ৭১০-এর দশকে সিন্ধু বিজয় করেছিলেন, এবং আলিপন্থী বিপ্লবী আল-মুখতার ইবনে আবি উবায়েদ।